১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু
—– শাহিদা আকতার জাহান
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে ও অনেক বৈষম্যের কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তার মধ্যে মূল বিষয় ছিলো ভূমি সংস্কার, অর্থনীতি, রাষ্ট্রভাষা, প্রশাসনের ক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাস। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাঙলিরা লাভ করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, নিজস্ব পতাকা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গেফতার হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর নিবিচারে গণহত্যা, চালায়। ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ নামক ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি সদরদপ্তর স্থাপন করা হয়।প্রথম সদর দপ্তরটি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। এখানে ৫৭তম বিগ্রেডের বিগ্রেডিয়ার আরবাবকে শুধু ঢাকা নগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এবং মেজর জেনারেল খাদিম রাজাকে প্রদেশের অবশিষ্টাংশে অপারেশন চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। অপারেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান।
২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা ওয়ারলেস বসানো জিপ ও ট্রাকে করে ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের সাঁজোয়া বহরটি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এক কিলোমিটারের মধ্যে ফার্মগেট এলাকায় ব্যরিকেডের মুখে পড়ে। রাস্তার এপাশ-ওপাশ জুড়ে ফেলে রাখা হয়েছিল বিশালাকৃতির গাছের গুঁড়ি। অকেজো পুরোনো গাড়ি ও অচল ষ্টীম রোলারও ব্যরিকেডের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো। কয়েকশ লোক প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দেওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলি দ্রুতই তাদের কণ্ঠ নিস্তদ্ধ করে দেয়। সেনাবাহনী সারা শহরে শুরু করে গণহত্যা।পাকিস্তানি সৈন্যরা রাস্তায়-ফুটপাতে যাকেই দেখতে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। সামনে যা কিছু চোখে পড়েছে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে সৈন্যদের ট্যাঙ্ক কামান ও বন্দুকের গোলায় ধ্বংস করে দিয়েছে বহু আবাসিক এলাকা। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মানুষের দোকান পাট, বাড়িঘরে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ঢুকে অনেক ছাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককেও ঐ রাতে হত্যা করে। পুরনো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে মূল্যবান জিনিস পত্র লুটপাট করে, মহিলাদের গণ-ধর্ষণ করে। নিরস্ত্র জনগণের উপর হামলা ও নির্বিচারে গণহত্যা অভিযান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর ২৬ শে মার্চ বাংলার আবালবৃদ্ধ বণিতা ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ পাকবাহিনীর হানাদার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারই পরিণিতিতে ৩০ লক্ষ শহীদ ২ লক্ষধিক মা-বোনের ইজ্জতভ্রষ্টের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে অংকিত হয় “বাংলাদেশ’।
একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পাওয়ার জন্য নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বীর-মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়া ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি অনেক বাহিনী সংগঠিত করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী, গফুর বাহিনী এবং ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী আফতাব বাহিনী, সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদার বরিশালে তাঁর বাহিনীকে সুসংগঠিত করেন। এ সকল বাহিনী স্থানীয়ভাবে সুসংগঠিত হয়ে নিজেরাই হানাদারবাহিনী বিরুদ্ধে জীবনবাজী রেখে যুদ্ধো করেন। সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেছে এমন উদাহরণ বাংলাদেশের বেলায় যতোটা প্রযোজ্য ততোটা বিশ্বের অন্যান্য কোন দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি ঘটেনি। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম,মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেক বেশিশক্তিশালী গৌরবোজ্জ্বলও ব্যতিক্রমধর্মী।পৃথিবীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। বেশির ভাগ দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে।
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সকল এলাকায় স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। এই অভ্যুত্থানে অংশ নেয় সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ। পাকবাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যাকে মোকাবেলার জন্য গড়ে তোলা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী প্রতিরোধ বাহিনী। পাকিস্তানি শত্রু সেনারা সংখ্যায় অনেক বেশি ও তারা ছিল অনেক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাই মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন মুক্তিসংগ্রামীদের একটি একক কমান্ডের অধীনে আনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে মাঠ পর্যায়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
১. তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর নিয়মিত সদস্যবৃন্দ।এরা আগে থেকেই অস্ত্র ব্যবহারে সম্মুখ সমরাভিযানে প্রশিক্ষিত ছিলেন।১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কয়েকজন ছাড়া সবাই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন। নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়। এর সংগঠক ছিলেন এয়ার কমোডর এ.কে খন্দকার। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ক্যাপ্টেন খালেক, সাত্তার, শাহাবুদ্দিন, মুকিত, আকরাম, শরফুদ্দিন এবং ৬৭ জন বিমানসেনা নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। তাদের সম্বল ছিল মাত্র কয়েকটি ডাকোটা, অটার টাইপ বিমান এবং অ্যালুভেট হেলিকপ্টার। অনুরূপভাবে, পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা নৌসেনাদের নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠিত হয়।এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল মাত্র ৬টি ছোট নৌযান। নিয়মিত ব্রিগেড, সেক্টর ট্রুপ ও গেরিলা বাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সুসংগঠিত ছিল।
২. সাধারণ মানুষ যাঁরা বাংলাদশে থেকে ভারতে গিয়ে ভারতের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অস্ত্রচালনা,বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার ও গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশলে প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ লাভ করার পর দেশে এসে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এদের বলা হতো ‘গণবাহিনী’।
৩. টাঙ্গাইলের বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর (বীর উত্তম) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কাদেরিয়া বাহিনীর। এদের অধিকাংশই প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ল্যান্স নায়েক কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে দেশের ভেতরই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করে শত্রু মোকাবিলা করেছেন।
৪.কেবল ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নতুনভাবে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।তারাই দেশাভ্যন্তরে না-ফিরে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। এদের পৃথকভাবে নাম দেওয়া হয়েছিল ‘মুজিব বাহিনী’। ভারতের সেনাবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল ওবানের সক্রিয় সহযোগিতায় মুজিব বাহিনী গঠিত হয়। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দেরাদুনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খান ছিলেন এই বাহিনীর সংগঠক।
১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জন্যে ঘর বাড়ি, আত্নীয়-স্বজন ছেড়ে,অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে, প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নিজের দেশের ভূখণ্ডকে শত্রুমুক্ত করতে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে। হাজার হাজার মানুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।
১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একক প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখাগরিষ্ঠ দলের নেতা হাওয়া পরও পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।এরপর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।
১৯৭১-এর ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এরমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্যা নিরসনের জন্য শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলাপ- আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা ব্যর্থ হয়ে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ৬-দফা বাংলার জনগণকে স্বাধীনতার প্রকৃত রাজনৈতিক পথটি বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ১৯৭১সালে জানুয়ারি-মার্চ-সময়ের মধ্যে বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যবদ্ধ করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার অগ্রিম ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে নেতা শেখ মুজিবুর রহমান অত্যান্ত সতর্ক ছিলেন। এই আন্দোলন পশ্চিমারা যেন কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপে চিত্রায়িত করতে না পারে। তিনি কঠোর সতর্কতার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বাধীনতা অর্জনে রূপান্তরিত করার। সেক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ আন্দোলন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না তাঁর কাছে।তাই তিনি ৭ মার্চ-পরবর্তী সময়ে জনগণকে সেই প্রস্তুতি গ্রহণের আহব্বান জানান। ২৫ মার্চের পর থেকে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর অলি গলি থেকে যুদ্ধো শুরু করে দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার স্পৃহায় জেগে ওঠে ঘুরে দাঁড়ায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ। অস্ত্রের সন্ধানে তারা বাড়ী ঘর, গ্রাম ও শহর ত্যাগ করে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ছুটে যায়।সেখানে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অনেকে দেশের অভ্যন্তরেই তা শুরু করে, গ্রামের নারী-পুরুষ, কিশোর, তরুণ নির্বিশেষে সকলেই এই যুদ্ধের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সাহায্যের হাত প্রশস্ত করে দিয়েছে। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে সকলেই যার যার অবস্থান থেকে নেমে আসে পশ্চিমাদের প্রতিরোধ করতে। স্বাধীনতার প্রতি জনগণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের নৈতিক প্রবিত্র দায়িত্ব মনে করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী ২৭ মার্চ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) পাকিস্তানিদের দ্বারা অত্যাচরিত ও ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারগুলো সীমান্তে বরাবর শরণার্থী শিবির স্থাপন করে দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এ শিবিরগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বাছাই করা হতো। দেশকে হানাদারের কবল থেকে মুক্ত করার অদম্য বাসনায় পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে যুদ্ধের কৌশল, অস্ত্র চালনা ও বিস্ফোরক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মাঝে ও পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু দালাল জামায়াত রাজাকার, আলবদর আলশামস দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের দালল হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।বাঙলি নারীদের ধর্ষণ করার জন্য পাকবাহিনীদের হাতে তুলে দিয়েছে।মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিহৃত করে তাদেরকে হত্যা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।তারা নিজেরা ও প্রত্যক্ষভাবে এই ঘৃণিত, জঘন্য কাজগুলো করেছে। বাঙলি হয়ে বাঙলি মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে।
১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত ও অনিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলো। অনিয়মিত বাহিনীরা গণবাহিনী নামে পরিচিত ছিলো।আর যারা নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো তারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রথমে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরে গণবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। গণবাহিনীর সদস্যদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠানো হতো। আর নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা সশস্ত্রবাহিনীর প্রথাগত যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। ‘জেড ফোর্স’ নামে পরিচিত।
১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন।৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অমৃতসর, শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণের পর থেকেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। তখনই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্দেশ আসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রত্যাঘাত করার জন্য। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।
কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপিত হয়। ১২ এপ্রিল থেকে এই সদরদপ্তর থেকে কার্যক্রম শুরু করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম.এ রব এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারকে যথাক্রমে চীফ অব স্টাফ এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। দেশকে একান্ত নিজেদের করে পাওয়ার জন্য জনগণের আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভব মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় গুণাবলি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর আর্দশ ও চেতনাগুলো। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীরা ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধু বীহিন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করা যাবে। তারা তখন উপলব্ধি করতে পারে নাই বঙ্গবন্ধুর সশরীর অনুপস্থিতিত না হলে ও তাঁর অন্তরাত্মা যেন বাংলার জনগণের মধ্যে বিরাজমান। বঙ্গবন্ধুর নামে গঠিত হলো প্রবাসী সরকার। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই অন্যদেশের আশ্রয়ভূমিতে এমন বিশাল প্রতিষ্ঠান ও আয়োজন হঠাৎ কোথা থেকে দাঁড়িয়ে গেল তা বুঝতে পারে নাই বাংলার জনগণ। সেই সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করছিলো তাকে বিস্ময়কর বললেও কম বলা হবে।এই সব সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তায়। আসলে জনগণের শক্তি কতো প্রবল হতে পারে তা ১৯৭১-সালের দীর্ঘ নয় মাসের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বাঙলি জাতি নিজেদের অধিকার পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উজাড় করে আত্মোৎসর্গ করার নজির বিশ্বের ইতিহাসে সব সময় পাওয়া যায় না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তেমন জাগরণে উজ্জীবিত হয়েছিলো নিজেদের স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য। ফলে ত্রিশ লাখ মানুষ যখন তাদের মহামূল্যবান প্রাণ বিলিয়ে দিলো তখন মনে হয়নি এদেশের মানুষ মৃত্যুতে সামান্য আক্ষেপ করেছে। প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ যেন দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করাকেই ব্রত হিসেবে তাদের প্রবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিয়েছিলো। এদেশের নারী সমাজের ওপর যে হত্যা র্ধষন বর্বর-নির্যাতন নেমে এসেছিলো তাতে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য তাদের কোনভাবে আত্মত্যাগ করার কথা নয়। বরং বাংলার প্রতিটি নারী সমাজ সবছেয়ে বেশি আত্নত্যাগ করেছে। মা তার সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে প্রিয় দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দেখার জন্য। বোন তার প্রিয় ভাইকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে। বাবা তার সন্তানকে হারিয়ে ও আত্মহারা হয়েছে স্বাধীন দেশের পতাকা উড়তে দেখে। এ এক বিস্মযকর অন্তরের দেশপ্রেম মা- মাঠির অনুভূতি। ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি মানুষ দেখিযে দিয়ে গেছেন। এই স্বাধীনতা বাঙলির জীবনের শ্রেষ্ট অর্জন সোনালি অধ্যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করেছিলো।চীন পাকিস্তানকে কৌশলগত সমর্থন দেয়েছিলো। পক্ষান্তরে, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশসমূহ এবং জাপান ও পশ্চিমের অনেক দেশের বাংলার সাধারণ জনগণের পাশে থেকে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন।
১৯৭১-এর সেই বিশাল ক্যানভাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখনোও সঠিকভাবে যথাযথভাবে লিখে জাতির সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। একটি দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত অর্জন কোনো একটি রাজনৈতিক জম্ন নিয়ে দলের অসূভ শক্তি প্রদর্শন করলে তাদের দখলে যাবার বিষয় হতে পারে না। কেউ একটি সেক্টরে যুদ্ধকরলে সে মহান স্বাধীনতার ঘোষক হতে পারে না।যে দলের নেতার নেতৃত্বে আন্দোলন, সংগ্রাম যুদ্ধো হয়েছে যুগের পর যুগ তারই অবদান লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় তিনিই বাঙলির “জাতির পিতা” শেখ মুজিবুর রহমান।১৯৭১ সালে ১০ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের এক সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার (অধিনায়ক) নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও সুবিধার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত ছিলেন।
১নং সেক্টর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালি জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধান ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান। পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: ঋষিমুখ (ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম); শ্রীনগর (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); মনুঘাট (ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); তবলছড়ি (সুবেদার আলী হোসেন); এবং ডিমাগিরী (জনৈক সুবেদার)। এই সেক্টরে প্রায় দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ই.পি.আর, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রায় দুই হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং গণবাহিনীর সংখ্যা ছিলো প্রায় আট হাজার। এই বাহিনীর গেরিলাদের ১৩৭টি গ্রুপে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।
২ নং সেক্টর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালি জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের বাহিনী গঠিত হয় ৪- ইস্টবেঙ্গল এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালির ইপিআর বাহিনী নিয়ে। আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে ছিল এ সেক্টরের সদরদপ্তর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং পরে মেজর এ.টি.এম হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে প্রায় ৩৫ হাজারের মতো গেরিলা যুদ্ধ করেছে। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা (মাহবুব এবং পরে লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবীর); মন্দভাব (ক্যাপ্টেন গাফফার); শালদানদী (আবদুস সালেক চৌধুরী); মতিনগর (লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম); নির্ভয়পুর (ক্যাপ্টেন আকবর এবং পরে লেফটেন্যান্ট মাহ্বুব); এবং রাজনগর (ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং পরে ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান)। এই সেক্টরের বাহিনীর অভিযানের ফলে কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যবর্তী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে পাক-বাহিনী সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিককালে এই এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকারে থাকে। এই সেক্টরের বাহিনীর অভিযানের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো বেলোনিয়া সূচিবুূ্যহ প্রতিরক্ষা। ১ নং ও ২ নং সেক্টরের বাহিনীর যৌথ অভিযানের ফলে ২১ জুন পর্যন্ত বেলোনিয়া সূচিব্যুহের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ২ নম্বর সেক্টরের কয়েকটি নিয়মিত কোম্পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করে। এই কোম্পানিগুলো ছিল সুবেদার লুৎফর রহমানের অধীনে বেগমগঞ্জ এলাকায় অভিযানরত নোয়াখালী কোম্পানি, সুবেদার জহিরুল আলম খানের অধীনে চাঁদপুর মতলব এলাকায় অভিযানরত চাঁদপুর কোম্পানি, ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর অধীনে ঢাকার মানিকগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ এলাকায় অভিযানরত এক বিশাল বাহিনী, এবং ক্যাপ্টেন শওকতের অধীনে ফরিদপুরে অভিযানরত এক বাহিনী। শহরাঞ্চলের গেরিলারা ঢাকা শহরে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করে।
৩ নং সেক্টর উত্তরে চূড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) থেকে সিলেট এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে.এম শফিউল্লাহ এবং পরে মেজর এ.এন.এম নূরুজ্জামান। দুই ইস্ট বেঙ্গল এবং সিলেট ও ময়মনসিংহের ইপিআর বাহিনী সমন্বয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরের সদর দফতর ছিল হেজামারা। এই সেক্টরের অধীনে ১৯টি গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। নভেম্বর মাস পর্যন্ত গেরিলার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা কুমিল্লা-সিলেট সড়কে কয়েকটি সেতু বিধ্বস্ত করে পাক বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাদের সবচেয়ে সফল আক্রমণ ছিল শায়েস্তাগঞ্জের নিকটে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইনের সাহায্যে একটি রেলগাড়ি বিধ্বস্ত করা। এই সেক্টরের দশটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: আশ্রমবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); বাঘাইবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); হাতকাটা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); সিমলা (ক্যাপ্টেন মতিন); পঞ্চবটী (ক্যাপ্টেন নাসিম); মনতলা (ক্যাপ্টেন এম.এস.এ ভূঁইয়া); বিজয়নগর (এম.এস.এ ভূঁইয়া); কালাছড়া (লেফটেন্যান্ট মজুমদার); কলকলিয়া (লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোরশেদ); এবং বামুটিয়া (লেফটেন্যান্ট সাঈদ)।
৪নং সেক্টর উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট থানা পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সিলেটের ইপিআর বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং পরে ক্যাপ্টেন এ রব। হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে আসামের মাসিমপুরে। সেক্টরে গেরিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার এবং নিয়মিত বাহিনী ছিল প্রায় ৪ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: জালালপুর (মাসুদুর রব শাদী); বড়পুঞ্জী (ক্যাপ্টেন এ. রব); আমলাসিদ (লেফটেন্যান্ট জহির); কুকিতল (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং পরে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক); কৈলাশ শহর (লেফটেন্যান্ট উয়াকিউজ্জামান); এবং কমলপুর (ক্যাপ্টেন এনাম)।
৫ নং সেক্টর সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং জেলার পূর্বসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে। আটশত নিয়মিত সৈন্য এবং পাঁচ হাজার গেরিলা সৈন্য সমন্বয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সুনামগঞ্জ ও ছাতকের অধিকাংশ জলাভূমি ছিল এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: মুক্তাপুর (সুবেদার নাজির হোসেন এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ফারুক); ডাউকি (সুবেদার মেজর বি.আর চৌধুরী); শেলা (ক্যাপ্টেন হেলাল; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহবুবর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ); ভোলাগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট তাহেরউদ্দিন আখুঞ্জী; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস.এম খালেদ); বালাট (সুবেদার গনি এবং পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও এনামুল হক চৌধুরী); এবং বড়ছড়া (ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন)। এই সেক্টরের বাহিনী সিলেট, তামাবিল ও সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে বেশ কিছুসংখ্যক সেতু বিধ্বস্ত করে। এই সেক্টরের সর্বাধিক সফল অপারেশন ছিল ছাতক আক্রমণ।
৬ নং সেক্টর সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত। প্রধানত রংপুর ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকটবর্তী বুড়ীমারিতে। এটিই ছিল একমাত্র সেক্টর যার হেড কোয়ার্টার ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০০ এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১ হাজার। এদের মধ্যে ছিল ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৯০০০ গণবাহিনী। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: ভজনপুর (ক্যাপ্টেন নজরুল এবং পরে স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার); পাটগ্রাম (প্রথমে কয়েকজন ই.পি.আর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার কমান্ড করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব নেন); সাহেবগঞ্জ (ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন); মোগলহাট (ক্যাপ্টেন দেলওয়ার); এবং চিলাহাটি (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল)। এই সেক্টরের বাহিনী রংপুর জেলার উত্তরাংশ নিজেদের দখলে রাখে।
মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হানাদার পাকসেনা।
৭ নং সেক্টর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত হয়। ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই বাহিনী ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে রাজশাহীতে প্রাথমিক অভিযান পরিচালনা করে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ. রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল বালুরঘাটের নিকটবর্তী তরঙ্গপুরে। ২৫০০ নিয়মিত সৈন্য ও ১২৫০০ গেরিলা সৈন্য সমন্বয়ে প্রায় ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই সেক্টরে যুদ্ধ করে। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: মালন (প্রথমে কয়েকজন জুনিয়র অফিসার এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর); তপন (মেজর নজমুল হক এবং পরে কয়েকজন জুনিয়র ই.পি.আর অফিসার); মেহেদীপুর (সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর); হামজাপুর (ক্যাপ্টেন ইদ্রিস); আঙ্গিনাবাদ (একজন গণবাহিনীর সদস্য); শেখপাড়া (ক্যাপ্টেন রশীদ); ঠোকরাবাড়ি (সুবেদার মোয়াজ্জেম); এবং লালগোলা (ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী)। এই সেক্টরের বাহিনী জুন মাসে মহেশকান্দা ও পরাগপুর এবং আগস্ট মাসে মোহনপুর থানা আক্রমণ করে বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে। হামজাপুর সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস তাঁর বাহিনী নিয়ে কয়েকটি পাকিস্তানী বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান এবং পার্বতীপুরের নিকটে একটি ট্রেন বিধ্বস্ত করেন।
সেক্টর নং ৮
কুষ্টিয়া, যশোর, দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ ছিল ‘সেক্টর নং ৮’ এর অন্তর্ভুক্ত। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরে ছিল ৭টি সাব-সেক্টর।
সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ – মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল- আগস্ট), মেজর এম.এ. মনজুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)বয়ড়া (ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা); হাকিমপুর (ক্যাপ্টেন সফিউল্লাহ); ভোমরা (ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন); লালবাজার (ক্যাপ্টেন এ আর আজম চৌধুরী); বনপুর (ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান); বেনাপোল (ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম, ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী); শিকারপুর (ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর)
সেক্টর নং ৯
পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় ‘সেক্টর নং ৯’। ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল ও তারপর মেজর জয়নাল আবেদীন এবং এছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন মেজর এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল ভারতের বসিরহাটের টাকিতে। এই সেক্টরে ছিল ৩টি সাব-সেক্টর।
দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা-মেজর এম.এ. জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর প্রথমার্ধ), মেজর জয়নুল আবেদীন(ডিসেম্বর এর অবশিষ্ট দিন) তাকি হিঞ্জালগঞ্জ শমসেরনগর
সেক্টর নং ১০
সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, নৌ কমান্ডো ও আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন ছিল ‘সেক্টর নং ১০’ এর অধিনে। এ সেক্টরে নৌ কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে মিশনে নিয়োজিত থাকতেন, তখন সে সেক্টরের কমান্ডারের নির্দেশে কাজ করতেন। এই সেক্টরে কোনো সাব-সেক্টর ছিল না এবং ছিল না নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়, নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি কর্মকর্তা এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন।নৌবাহিনীর কমান্ডো দ্বারা গঠিত। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হত।
সেক্টর নং ১১
কিশোরগঞ্জ বাদে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত হয় ‘সেক্টর নং ১১’। এপ্রিল থেকে ৩ই নভেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম আবু তাহের ও তারপর ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট এম হামিদুল্লাহ। আর এই সেক্টরের সদর দপ্তর হিসেবে ভারতের আসামের মহেন্দ্রগঞ্জকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই সেক্টরকে ৭টি সাব-সেক্টর ভাগ করা হয়েছিল।
কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল – মেজর আবু তাহের (আগস্ট-নভেম্বর), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম. হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মানকারচর (স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান); মাহেন্দ্রগঞ্জ (মেজর আবু তাহের; লেফটেন্যান্ট মান্নান); পুরাখাসিয়া (লেফটেন্যান্ট হাশেম); ধালু (লেফটেন্যান্ট তাহের; লেফটেন্যান্ট কামাল); রংগ্রা (মতিউর রহমান) শিভাবাড়ি (ই পি আর এর জুনিয়র কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় ); বাগমারা (ই পি আর এর জুনিয়র কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় ); এবং মাহেশখোলা (ই পি আর এর জনৈক সদস্য) টাংগাইল সেক্টর – সমগ্র টাংগাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার অংশ – কাদের সিদ্দিকী ।আকাশপথ – বাংলাদেশের সমগ্র আকাশসীমা – গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।
মাতৃভূমিকে শত্রু মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের সমস্ত যুদ্ধাঞ্চল কে ১১ টি সেক্টর বিভক্ত করা হয়। শেরপুর ছিল ১১ নং সেক্টরের অধীনে। ১১ নং সেক্টর গঠিত হয় কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল নিয়ে। ১১ নং সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর আবু তাহের (এপ্রিল থেকে নভেম্বর)। মহান মুক্তিযুদ্ধ কে আরও ফলপ্রসূ করতে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের এ অঞ্চল কে কয়েকটি সাব সেক্টরে ভাগ করেন:
১. মানকারচর সাব-সেক্টর।
২. মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর।
৩. পুরা খাসিয়া সাব-সেক্টর।
৪. ডালু সাব-সেক্টর।
৫. রংরা সাব-সেক্টর।
৬. শিববাড়ি সাব-সেক্টর।
৭. বাগমারা সাব-সেক্টর।
৮. মহেশখোলা/মহেশখালী সাব-সেক্টর।
১৯৭১ সালে ১৫ নভেম্বর পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের গুরুতর আহত হন। পরে স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) এ সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।
তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন মাতৃভূমি থেকে শত্রু বিতারিত করতে। তিনি বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন।
বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধা ছিলেন শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, তিনিও ১১ নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর।
১১ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার প্রথমে ছিল লেলডালা এবং পরে ১০ অক্টোবর ১৯৭১ সালে মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম, ভারত স্থানান্তর করা হয়।
ভারতীয় সৈন্য এবং এগারো নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার টঙ্গীর কাছে পৌঁছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে তারা সাভারে অবস্থান নেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৬ নম্বর ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জমশেদ ঢাকা নগরীর সন্নিকটে মীরপুর সেতুর কাছে ভারতীয় অধিনায়ক মেজর জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানান। সকাল দশটায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকায় প্রবেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খসড়া দলিল নিয়ে অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এক হেলিকপ্টার বহরে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিকাল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ-ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার। পরাজিত পাকিস্তানি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজী লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরাকে আত্মসমর্পণসূচক অভ্যর্থনা জানান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কম্যান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।
(লেখকঃ শাহিদা আকতার জাহান
সদস্য, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।
নির্বাহী সদস্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগ
সিনিয়র সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা মহিলা আওয়ামীলীগ।
সভাপতি, চট্টগ্রাম দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা এবং
“বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা ও বিশ্বভাবনা” এবং “অপ্রতিরোধ্য শেখ হাসিনা” গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।
——-
[লেখকের তথ্য ও ভাষা শৈলি হুবহু ঠিক রেখেই প্রকাশিত হয়েছে]
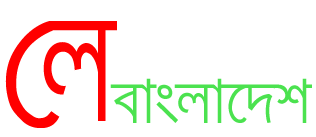








 Users Today : 137
Users Today : 137 This Month : 2941
This Month : 2941 This Year : 16113
This Year : 16113 Total views : 134259
Total views : 134259